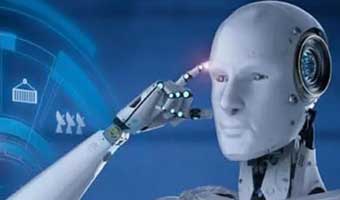কাজী জহিরুল ইসলাম
কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতার ভাষাশৈলী
আবু তাহের সরফরাজপ্রকাশিত : ডিসেম্বর ১২, ২০২৫
কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতার ভাষাশৈলী বুঝতে হলে আমাদের চোখ রাখতে হবে তার কবিতার অন্তর্গত বোধের বিন্যাসে। কী রূপে, কী উপায়ে তিনি তার বোধকে ভাষায় প্রকাশ করছেন, সেই সক্ষমতার দিকে। কারণ, যে কবিতায় শব্দের কারুকাজ যত নিখুঁত, সেই কবিতার শরীর থেকে শিল্পের সৌন্দর্য পাঠকের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শব্দের যথেষ্ট বুনন নয়, বরং শব্দ ব্যবহারের পরিমিতিবোধেই কবিতায় শব্দের কারুকাজ নান্দনিক হয়ে ওঠে। জহিরুলের কবিতা পড়তে-পড়তে পাঠক সহজেই কবিতার অন্তর্নিহিত গহনে ডুব দিতে পারে। কারণ, তার কবিতায় শব্দের ওপর জোরপ্রয়োগ নেই। মানে, প্রকাশের দায় থেকে কবিতার অবয়বে শব্দ যেন নিজের থেকেই জায়গা করে নেয়। সেসব কবিতা পাঠে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, কবিতা তিনি লেখেননি। কবিতাই তাকে মাধ্যম করে নিজেকে প্রকাশ করেছে।
শব্দ বুননের মুনশিয়ানায় কাজী জহিরুল ইসলাম জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী। কী বলছেন তার দিকে খেয়াল রেখে তিনি বলার কথাকে এমন কৌশলে শব্দের বাহনে চড়িয়ে দেন যে, তার সৃষ্ট শব্দযান চলতে শুরু করে তরতর গতিতে। এই গতির প্রভাবে পাঠকও গতি পেয়ে যায়। পাঠককে গতিশীল করে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। ভীষণ কঠিন কর্ম। কঠিন এই কর্মটি কাজী জহিরুল ইসলাম খুব স্বচ্ছন্দ্যেই করে থাকেন। যেন বিষয়টি তার স্বভাবসিদ্ধ। আমরা জানি, শব্দ যে-কোনো একটি মানে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকৃত কবির কবিতায় মানে বহন করা ছাড়াও কবির বোধের স্পন্দন অনুরণিত হয়ে ওঠে শব্দে। মহাজাগতিক অন্তর্বোধ যে-কোনো কবির বড় সম্পদ। জীবন ও জগৎকে পর্যবেক্ষণ খুব সূক্ষ্মভাবে করতে না পারলে কবির কবিতা হয়ে ওঠে মোমবাতির আলোর মতো। পাঠকের অন্তর্জগতের খুবই অল্প একটু জায়গাই ওই কবিতা দ্বারা আলোকিত হয়।
কিন্তু আমরা জানি, মানুষের বোধের জগতের বিস্তৃতি মহাবিশ্বের মতো। সেই জগৎকে কবিতার আলো ফেলে দেখার চেষ্টা কাজী জহিরুল ইসলাম তার অনেক কবিতাতেই করেছেন। ‘মহাকালের ঘড়ি’ কবিতাটি পড়া যাক:
মেঘের নিচে দালান সারি-সারি
ক্লান্ত ডানা সন্ধ্যারেখায় খোঁজে আপন বাড়ি।
ঝিরিঝিরি বইছে হাওয়া ধীরে
যেতে-যেতে আলোর রেখা তাকায় ফিরে-ফিরে।
রঙের খেলা, আকাশ কোজাগরী
ঘণ্টা বাজায় কোথাও কি এক মহাকালের ঘড়ি?
সন্ধে নামছে। এই দৃশ্য শব্দে-শব্দে ভাষাচিত্রে অঙ্কিত করছেন কবি। আমাদের সকলেরই পরিচিত সন্ধের নৈসর্গিক দৃশ্য। কর্মস্থল থেকে ক্লান্ত মানুষ ফিরছে যার-যার বাড়ি। হাওয়া বইছে ঝিরঝির। দিনের শেষ আলোটুকু পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে যেতে-যেতে যেন একটুখানি পেছন ফিরে দেখে নেয়। এরপর গোধূলির রঙছবি শব্দের বর্ণনায় এঁকেছেন কবি। যেন রঙের খেলা! এই খেলায় আকাশ জেগে উঠেছে। তাই আকাশকে কবি বলছেন, কোজাগরী। সন্ধের এই নির্জন সমাহিত রূপ দেখে কবির হঠাৎই মনে হয়, কোথাও যেন ঘণ্টা বাজাচ্ছে মহাকালের ঘড়ি। মহাকালের ঘড়ি এখানে প্রতীকী। এই প্রতীকের আড়ালে আসলে মৃত্যুর কথাই বলতে চেয়েছেন কবি। মনে পড়ছে জসীম উদদীনের সেই বিখ্যাত পঙক্তি: আজান হাঁকিছে মসজিদ হতে বড় সকরুণ সুর/মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর। সন্দেহ নেই, এই আজান মাগরিবের আজান। সন্ধের রূপটাই আসলে করুণ।
পুরোটা দিন পৃথিবীকে আলোকিত রেখে সন্ধের ফিকে অন্ধকার একটু-একটু করে মুছে দেয় আলো। পৃথিবীর বুকে নেমে আসে অন্ধকার। এই অন্ধকার জীবনের নিরাশার পিঠ। আর আলো জীবনের আশা আর সম্ভাবনার পিঠ। কাজী জহিরুল ইসলাম নতুন কোনো ইঙ্গিত এই কবিতায় না-দিলেও স্বরবৃত্ত ছন্দে সন্ধের যে রূপ এঁকেছেন, সেই রূপ শৈল্পিক সুষমায় অনন্য। শব্দের বুননে ভাষার যে শৈলীতে সন্ধের রূপ কবি চিত্রিত করেছেন, সেই ভাষাশৈলী যেন সন্ধের রঙমাখা তুলির আঁচড়। কবিতার অবয়বে যেন শব্দ নয়, রঙ-মাখানো তুলির এক-একটি প্রলেপ। ভাষার এহেন শৈলী কবিতার গহনে লুকিয়ে থাকা কবির অন্তর্বোধকে প্রকাশ করে প্রাঞ্জল উপায়ে। এই কৃৎকৌশল জহিরুলের দীর্ঘদিনের কাব্যচর্চার ফসল।
আশি কিংবা নব্বইয়ের দশকের কবিদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। কিন্তু আমরা দেখি যে, হাতেগোণা মাত্র কয়েকজন কবিই কেবল পেরেছেন ভাষার স্বকীয় শৈলী ও কাব্যনির্মাণ কাঠামো তৈরি করে নিতে। আসলে মানুষের বলার কথা খুব বেশি বিস্তৃত নয়। ঘুরেফিরে কিছু কথাই যুগে-যুগে মানুষ কবিতার ভেতর দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছে। তবে সেসব কবিতার ভেতর অল্প সংখ্যক কবিতাই কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও পাঠকের কাছে আদৃত। এর কারণ প্রধানত দুটি। এক. কবির অন্তর্জগতের দার্শনিক প্রজ্ঞাসঞ্জাত উপলব্ধির শৈল্পিক প্রকাশ। দুই. সেই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কবিতার ভাষাশৈলী। মূলত ভাষাই একটি কবিতার শারীরিক কাঠামো নির্মাণ করে। কাঠামো ছাড়া কোনো কিছুই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে প্রকাশ পায় না। সেই কাঠামো যত বেশি শিল্পোৎকর্ষতা ধারণ করে ওই কাঠামো তত বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।
কাজী জহিরুলের স্বকীয় ভাষাশৈলীতে নির্মিত কবিতাগুলোর কাঠামো এই কারণেই পাঠকনন্দিত। তিনি জানেন, কোন কথা কোন ভাষাভঙ্গিতে ব্যক্ত করতে হয়। ফলে, তার একেকটি কবিতার বইয়ের কবিতাগুলোতে বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে ভাষারীতিকে তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলেন। বলার কথার সঙ্গে ভাষাশৈলীর সংমিশ্রণে তিনি যেন ঐন্দ্রজালিক কোনো শিল্প-নৈপুণ্য ব্যবহার করেন। তার কবিতার শব্দগুলো প্রাণস্পন্দনে সজীব। নীরস নয়, কাঠখোট্টা নয়। তার কবিতার শব্দেরা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। প্রতিদিনের পরিচিত আটপৌরে শব্দের বুননে নির্মিত তার কবিতার নকশিকাঁথা। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, শব্দ কিন্তু কবিতার প্রধান শক্তি। শব্দের সারল্য না থাকলে কবিতা সৌন্দর্য হারায়। একটি অট্টালিকা যেমন ইট ও সিমেন্টের গাঁথুনি নিয়ে গড়ে ওঠে, একইভাবে কবিতাও শব্দ ও বোধের গাঁথুনি নিয়ে গড়ে ওঠে। এখানে আমি বলতে চাচ্ছি, শব্দ হচ্ছে ইট আর সিমেন্ট হচ্ছে কবির অন্তর্লীন বোধ। যে-কোনো শব্দকে বোধের রসায়নে জারিত করেই কবিকে নির্মাণ করতে হয় কবিতার অট্টালিকা।
এ প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসকে স্মরণ করছি। সম্রাট বিক্রমাদিত্য সভাসদদের নিয়ে রাস্তায় হাঁটছেন। সঙ্গে বিদ্যাপতি ও কালিদাসও রয়েছেন। বলে রাখা ভালো, বিদ্যাপতি কালিদাসকে খুব হিংসে করতেন। গোপাড় ভাঁড়ের পেছনে যেমন সবসময় মন্ত্রী লেগে থাকতো, সেই রকম। যাই হোক, হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ সম্রাটের চোখে পড়লো, রাস্তার পাশে শুকনো একটা গাছ পড়ে আছে। সম্রাট বিদ্যাপতিকে জিগেশ করলেন, ওহে বিদ্যাপতি, বলো তো ওই ওখানে ওটা কী পড়ে আছে? নিজের কবিত্ব জাহির করার সুযোগ পেয়ে বিদ্যাপতি বললেন, শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে। মানে, একটি শুকনো কাঠ সামনে পড়ে আছে। সম্রাট এবার একই প্রশ্ন কালিদাসকে জিগেশ করলেন। কালিদাস জবাব দিলেন, নীরস তরুবর পূরত ভাগে। মানে, একটি রসহীন (শুকনো) গাছ সামনে পড়ে আছে। সম্রাট সভাসদদের প্রত্যেককে জিগেশ করলেন, কার জবাব বেশি শ্রুতিমধুর। সকলেই কালিদাসের পক্ষে রায় দিলেন।
এই গল্প বলার উদ্দেশ্য, একই কথা নানাজনে নানা রকমভাবে বলতে পারে। কিন্তু কবি যখন বলেন তখন তা যেন কানে মধু ঢেলে দেয়। শব্দের জাদু এখানেই। আমরা দেখি যে, কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতায় কী এক জাদুর ঘোরে শব্দগুলো নিজেই দ্যোতনা প্রকাশ করে। নিজে-নিজেই শব্দ যখন পাঠকের বোধের সামনে নিজেকে মেলে ধরে, পাঠক তখন সহজেই ওই শব্দের অর্থময়তা ও দৃশ্যকল্প তার অন্তর্গত বোধের রসায়নে জারিত করে তুলতে পারে। যে-কোনো ভালো কবিতার প্রসাদগুণ এখানেই। ‘অন্ধকারে জিহ্বা নাড়ে পাপের গহ্বর’ বইয়ের ‘সহস্রাব্দের পাখি’ কবিতা থেকে কয়েক পঙক্তি পড়া যাক:
রাত্রির যুগল ভ্রুর মাঝখানে জেগে
ওঠে সমৃদ্ধি-প্রবণ সূর্য
সহস্রাব্দের পাখিরাই ওকে ডেকে তোলে
এবং ঠেলে দেয় কর্পোরেট আকাশে।
নৈবেদ্যের থালায় যে সংশয়
রোজ অজান্তেই জমা হয় মহন্তের,
সেই মেঘ,
সেই ছায়া, ঢেকে দেয় দুপুর, বিকেল...
তটরেখায় বিস্তৃত ভ্রুর নিচে
দুটি নদী
টলমল করে আসন্ন সন্ধ্যায়।
এই যে পঙক্তিগুচ্ছ আমরা পড়লাম, এখানে এমন একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে শব্দটি মনে হতে পারে জোর-জবরদস্তি করে নামিয়ে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। বরং দেখা যাচ্ছে, শব্দের চৌম্বকীয় আকর্ষণে একটি শব্দ আরেকটি শব্দের সাথে বাঁধা পড়ে আছে। কবিতার এরকম কৃৎকৌশল কিন্তু সহজাত। ভেতর থেকে উঠে আসতে হয়। তা না-হলে নিখুঁত জ্যামিতিক ছকে কবিতাকে শিল্পরূপ দেয়া কঠিন। জোর করে শব্দকে ধরে এনে এ ধরনের কবিতা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। দিন ও রাতের আবর্তনে বৈজ্ঞানিক যে ব্যাখ্যা আমরা জানি সেই ব্যাখ্যার পাশাপাশি এই কবিতায় আরেক রকম চমকপ্রদ বর্ণনা কবি দিচ্ছেন। এই বর্ণনার ভাষাচিত্রে শব্দকে শব্দের নিজস্ব মানে থেকে বের করে এনে জহিরুল ছড়িয়ে দেন বিশেষ কয়েকটি ব্যঞ্জনায়।
পাঠক তার বোধ ও কল্পনা-প্রসারণের ক্ষমতা অনুযায়ী ওইসব শব্দের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে কবির বিশেষ শিল্পপ্রয়াস এখানেই যে, তিনি পাঠকের সামনে বিস্তৃত ক্যানভাস মেলে ধরেন। সেই ক্যানভাসে ভাষাচিত্রে কয়েকটি আঁচড় দিয়ে দাগ কেটে রাখেন। এরপর পাঠকের মনোভূমে অন্তর্বোধের শৈল্পিক চিত্রময়তা নির্মিত হয়। দেখা যাচ্ছে, ভাষার এই কারুকাজ জহিরুলের কবিতাকে তার সময়ের আরসব কবি থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করে দিয়েছে। ফলে, তার যে-কোনো কবিতাপাঠে পাঠক সহজেই বুঝতে পারে, এই কবিতা কাজী জহিরুল ইসলামের না-হয়ে পারেই না।
লক্ষ্যণীয় যে, শব্দের জাঁকজমকে তার কবিতার ইঙ্গিত চাপা পড়ে থাকে না। তার কবিতায় ইঙ্গিত প্রকাশ্য, একইসঙ্গে শব্দের জাঁকজমকও প্রকাশ্য। এখানে জাঁকজমক বলতে আমি আসলে বোঝাতে চাইছি, শব্দের শিল্পসৌন্দর্য। শব্দের জৌলুশ নয়। শব্দের জৌলুশ দিয়ে জহিরুল পাঠকের চোখ ঝলসে দিতে আগ্রহী নন। বরং তার আগ্রহ, পাঠকের বোধের জগৎকে উজ্জীবিত করা। পাঠককে স্থবিরতা থেকে প্রাণস্পন্দনে সজীব করে তোলা। কবিতার ভেতর দিয়ে জহিরুল পাঠকের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করতে চেষ্টা করেন। আর তার জন্য তিনি তৈরি করেন শব্দের সাঁকো। সুতরাং, শব্দকে তিনি স্বভাগত শিল্পকুশলতায় সংযত করেন। আর এ কারণেই পাঠক সহজেই কবিতার ভেতর ডুব দিতে পারে। সহজেই বুঝতে পারে কবিতার ইঙ্গিত। ভাবের ওপর কবিতার শব্দকে তিনি বসান না। ভাব যা থাকে তা আসলে শব্দের প্রলেপ হিসেবে থাকে।
ভাষার ভেতর দিয়ে কাজী জহিরুল ইসলাম তার অন্তর্বোধের সংকেত কবিতায় কী উপায়ে রোপণ করেন, সেদিকে এবার একটু চোখ রাখা যাক। অন্তর্জগতের অন্তর্লীন অনুভূতি প্রকাশে কবিতার ভেতর দিয়ে যে পর্যটন তিনি করেন সেই যাত্রায় তার বিন্যাস্ত শব্দেরা স্বাভাবিক গতিতেই কবির সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে কবিতার শরীরে গ্রোথিত হয়। আর, এসব শব্দের ভেতর কোষ্ঠকাঠিন্য নেই। আছে সরলরেখার মতো সরলতা। আছে সহজেই শব্দের প্রাণস্পন্দন অনুভব করার প্রাঞ্জলতা। শব্দের ভেতর দিয়ে নিঃসীম এক ধরনের অনুভূতি জহিরুল আমাদের ভেতর ছড়িয়ে দেন। কবিতার ভেতর দিয়ে আসলে তিনি ধ্যান করেন। ধ্যানের মগ্নতা পাওয়া যায় তার প্রতিটি কবিতায়। শব্দ যেন তার হাতের তসবিহর দানা। বোধের ভাষারূপ দিতে কবিতার শরীরে একটি শব্দ বসানো মানে, তসবিহর এক একটি দানা তিনি ভক্তিভরে উচ্চারণ করেন।
কবিতার প্রতি এই নিবিষ্টতা যে-কোনো কবির আত্মার শুদ্ধতাকে উন্মোচিত করে আমাদের শৈল্পিক দৃষ্টির সীমানায়। কবিতা তো একঅর্থে আত্মার কাতরতা। যত মানুষ, তত আত্মা। এজন্য দেখি যে, আত্মরূপ দর্শনের গভীর উন্মোচন ঘটেছে তার কোনো কোনো কবিতায়। এই উন্মোচনে ভাষার শৈলীও শিল্পের অনন্য ভঙ্গিমায় সংযোজিত। বলতে কী, জহিরুল কবিতার স্বভাবজাত জাদুকর। তার বোধের জগৎ শব্দদৃশ্য শোভাকর। কখনও তার কবিতার শব্দ জাদুময়ী ঘোর তৈরি করে, আবার কখনও খুবই আটপৌরে যাপিতজীবনের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। মূলত কবিতার ভেতর দিয়ে তিনি পাঠকের বোধকে উজ্জীবিত করে তোলেন। তার কবিতার শব্দগুলো অনুভূতিকে ভাষারূপ দিতে গার্ড অব অনার দিতে-দিতে নিজ থেকেই এগিয়ে আসে।
কাজী জহিরুল ইসলামের বেশকিছু কবিতায় বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার আমাদের চোখে পড়বে। বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃতির জ্ঞান। আর কবিতা হচ্ছে অন্তর্জগতের উপলব্ধির ভাষারূপ। বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট ও পরীক্ষালব্ধ। বিপরীতে, কবিতা অনির্দিষ্ট এবং পরীক্ষার ধার ধারে না। সুতরাং, বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট শব্দ যখন কবিতার মতো অনির্দিষ্ট মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় তখন ওই শব্দ কী অর্থ প্রকাশ করছে, কিভাবে করছে, সে বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের আগ্রহ তৈরি হয়। কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতায় প্রচুর বৈজ্ঞানিক শব্দ চোখে পড়ে। অবাক হয়ে দেখি যে, সেসব শব্দকে নির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে বের করে এনে তিনি আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যে নানা মাত্রিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মনেই হচ্ছে না, শব্দগুলো বিজ্ঞানের। বরং মনে হচ্ছে, এসব শব্দ বুঝি কবিতায় ব্যবহৃত হতেই সৃষ্টি হয়েছে। ‘বালিকাদের চাবিওয়ালা’ বইয়ের ‘হাতগুলো’ কবিতা থেকে কয়েক পঙক্তি পড়া যাক:
হাতগুলো চোখ, দৃষ্টি দৃশ্যবৃত্তের বাইরে
ঘাসের মাঠ থেকে ধূসর হিরোশিমা
জিরোসীমা থেকে ইনফিনিটি আকাশ-নীল ও নক্ষত্রমণ্ডলী
কজন অণুবীক্ষণ, নভোমণ্ডল থেকে
নামিয়ে আনছে অচেনা বৃক্ষের ফল,
ফেরি করছে আকাশ-হাটে প্রতি এলিয়েনবারে।
বিশ্ব-রাজনীতির আগ্রাসী থাবার চিত্র এখানে আমরা পাচ্ছি। আমরা জানি, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে-সাথে আগ্নেয়াস্ত্রের আধুনিকায়ন ঘটে। বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের চেয়ে অকল্যাণে ব্যবহারেই বেশি পারদর্শী পশ্চিমা দেশগুলো। প্রযুক্তির বদৌলতে মানুষের ক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে গেছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটছে মানুষ। কবি বলতে চাচ্ছেন, এই ছোটার পেছনে সভ্যতার অগ্রগতির চেয়ে ব্যবসায়িক মনেবৃত্তিই মানুষকে বেশি প্ররোচিত করছে। গোটা কবিতাটি পড়লে বিষয়টির গভীরে ঢুকে পাঠক এই কথার মর্ম পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারবে। আরও কয়েকটি কবিতায় বৈজ্ঞানিক শব্দকে যেভাবে জহিরুল কবিতার শরীরে গেঁথে দিয়েছেন সেই কৌশল তার ভাষাশৈলীকে শৈল্পিক উৎকর্ষে অনন্য করে তুলেছে। তবে সম্ভাবনা থাকে যে, এসব বৈজ্ঞানিক শব্দপাঠে সাধারণ পাঠক হোঁচট খেতে পারে। বিরক্তও হতে পারে। কিন্তু যেসব পাঠক শব্দগুলোর বৈজ্ঞানিক মানে ব্যাখ্যাসহ জানেন তারা বিস্মিত হয়ে দেখবেন যে, শব্দগুলো বিজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে মানবিক বোধের অসীমে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় নানা অর্থ প্রকাশ করছে।
এসব অর্থের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মানুষের বোধের অতলান্তিক জগৎ। এই হিসেবে অবশ্য বলা যেতেই পারে, জহিরুলের কবিতা শিক্ষিত পাঠকের জন্য। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে রুচিমান পাঠকের জন্য। আবার এও সত্যি, এ ধরনের কবিতা খুব বেশি জহিরুল লেখেননি। তার বেশির ভাগ কবিতা ভাষার প্রাঞ্জলতায় বহমান সমুদ্রের মতো। সমুদ্রে যেমন অথই জলরাশি তেমনই তার কবিতায় শব্দের ভাঁজে-ভাঁজে মানুষের নিঃসীম অন্তর্জগতের প্রগাঢ় উপলব্ধি।